এক পণ্যের ওপর ভরসায় দেশের ভবিষ্যৎ
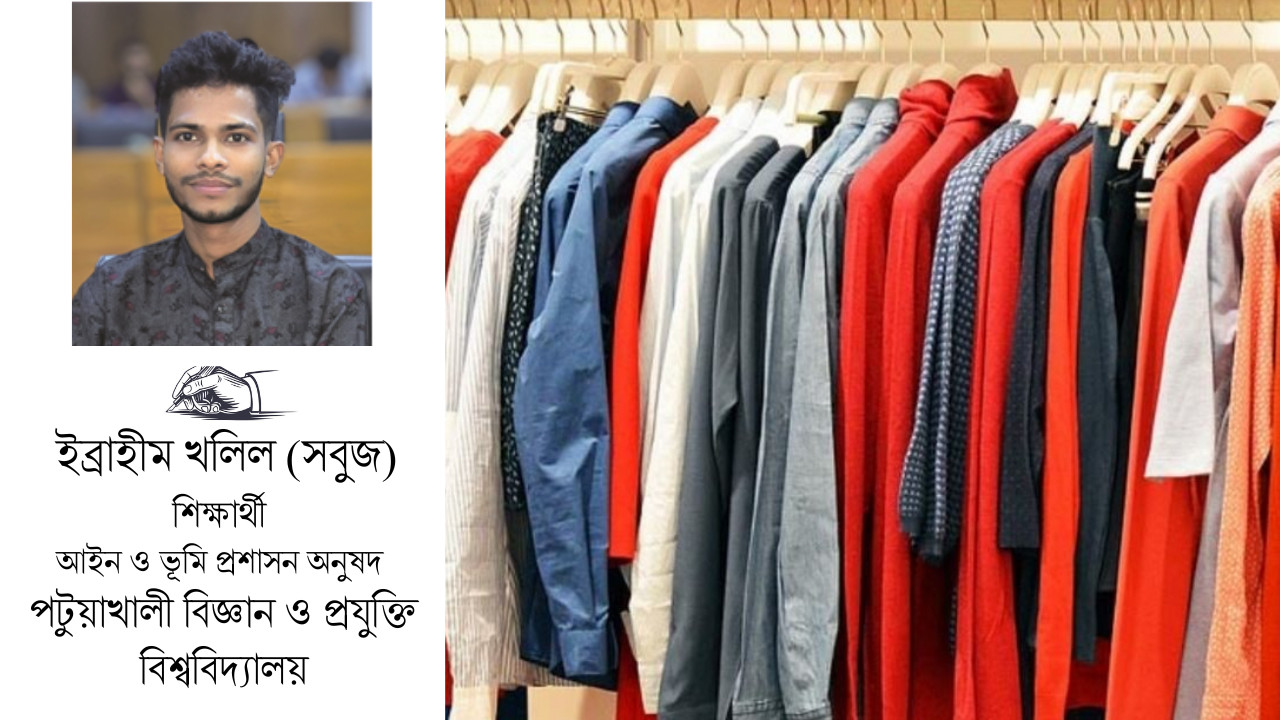
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সাফল্যের গল্প বলতে গেলে প্রথমেই চলে আসে তৈরী পোশাকশিল্পের নাম। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে তৈরি পোশাক বা গার্মেন্টস খাতই দেশের রপ্তানি আয়ের প্রাণকেন্দ্র। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয় ছিল প্রায় ৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে পোশাক শিল্পের অবদান প্রায় ৪৭ বিলিয়ন। বর্তমানে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৪ শতাংশ আসে এই একটি খাত থেকে। এই শিল্পই গ্রামীণ নারীদের শ্রমবাজারে যুক্ত করেছে, লাখো মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করেছে, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। কিন্তু এই সাফল্যের পেছনেই লুকিয়ে আছে এক বড় ঝুঁকি রপ্তানি আয়ে বৈচিত্র্যের অভাব। একটি দেশের রপ্তানি খাত যত বৈচিত্র্যময় হয়, তত বেশি স্থিতিশীল হয় তার অর্থনীতি। কারণ, বৈশ্বিক বাজারের যে কোনো ওঠানামা তখন সহজে সামাল দেওয়া যায়। কিন্তু বাংলাদেশের বাস্তবতা ঠিক উল্টো। তৈরি পোশাক খাতের ওপর অতিনির্ভরতার ফলে পুরো অর্থনীতি হয়ে পড়েছে ঝুঁকিপূর্ণ। যখন ইউরোপ বা যুক্তরাষ্ট্রে পোশাকের চাহিদা কমে যায়, বা বৈশ্বিক মন্দা দেখা দেয়, তখন সরাসরি আঘাত পড়ে বাংলাদেশের বৈদেশিক আয়ের ওপর। ২০২০ সালের কোভিড-১৯ মহামারির সময় এই খাতের রপ্তানি হঠাৎ ১৮ শতাংশ পর্যন্ত কমে গিয়েছিল। ফলে হাজার হাজার কারখানা বন্ধ হয়ে যায়, লাখো শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতি কেবল একবারের ধাক্কা নয়; এটি ভবিষ্যতেরও সতর্কবার্তা। কারণ বিশ্ব বাজার এখন ক্রমেই প্রতিযোগিতামুখী ও প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অটোমেশন ও সাপ্লাই চেইনের পুনর্গঠন সব মিলিয়ে পোশাক খাতে কম খরচের সুবিধা আগের মতো কার্যকর নাও থাকতে পারে। এর আরেকটি বড় সমস্যা হলো যুব সমাজের কর্মসংস্থান সংকুচিত হওয়া। গার্মেন্টস খাতেই দেশের ৪০ লাখের বেশি মানুষ কাজ করলেও, উচ্চশিক্ষিত তরুণদের জন্য এই খাতে উপযুক্ত জায়গা নেই। ফলে নতুন শিল্পখাত না গড়ে উঠলে “মিডল ইনকাম ট্র্যাপ” থেকে বের হওয়া কঠিন হবে।
বাংলাদেশের রপ্তানি মূলত ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আমেরিকা-কেন্দ্রিক। মোট রপ্তানির প্রায় ৭৫ শতাংশই যায় এই দুটি বাজারে। ফলে ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের অভাবও অর্থনীতিকে অরক্ষিত রাখছে। আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য বা পূর্ব এশিয়ার বাজারে বাংলাদেশের উপস্থিতি প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ এই অঞ্চলগুলোই হতে পারে ভবিষ্যতের বড় ক্রেতা। ভারতের মতো প্রতিবেশী দেশ ইতোমধ্যেই আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় নতুন বাণিজ্য নেটওয়ার্ক তৈরি করছে। ভিয়েতনাম একসময় বাংলাদেশের মতোই গার্মেন্টস রপ্তানির ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিন্তু গত এক দশকে তারা ইলেকট্রনিকস, মোবাইল অ্যাসেম্বলি, কৃষি-প্রসেসিং ও আইটি খাতে রপ্তানি বাড়িয়ে আয়ের কাঠামোকে বৈচিত্র্যময় করেছে। বর্তমানে ভিয়েতনামের রপ্তানি আয়ের ৪৫ শতাংশের বেশি আসে নন-টেক্সটাইল খাত থেকে। অন্যদিকে মালয়েশিয়া পাম তেল, ইলেকট্রনিকস ও সেবা খাতে সমন্বিত রপ্তানি কাঠামো গড়ে তুলেছে। ইথিওপিয়া আফ্রিকায় নতুন শিল্পাঞ্চল তৈরি করে পোশাক ছাড়াও চামড়া ও কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানিতে জোর দিচ্ছে। বাংলাদেশ এখনো সেখানে পৌঁছায়নি। যদিও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে রপ্তানি বাড়ছে ২০২৩ সালে প্রায় ৬০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার তবুও এটি সামগ্রিক রপ্তানির মাত্র ১ শতাংশের মতো। এই অমিলই বাংলাদেশের অর্থনীতিকে “এক পায়ে দাঁড়ানো” অবস্থায় রেখেছে।
বাংলাদেশে রপ্তানি বৈচিত্র্য বাড়ানোর উদ্যোগ নতুন নয়। চামড়া, ওষুধ, জাহাজ নির্মাণ, আইটি, কৃষিপণ্য সবই আলোচনায় এসেছে বহুবার। কিন্তু বাস্তবে এগুলোর রপ্তানি আয় এখনো নামমাত্র। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে ওষুধ খাতের রপ্তানি আয় ছিল প্রায় ২২ কোটি ডলার, আইটি খাতে ৭৫ কোটি ডলার, আর কৃষিপণ্যে ১.২ বিলিয়ন ডলার। এসবের তুলনায় তৈরি পোশাকের আয় প্রায় ৪৭ বিলিয়ন ডলার এক বিশাল ব্যবধান। এখানে মূল সমস্যা দুটি প্রণোদনা কাঠামো ও নীতিগত অগ্রাধিকার। সরকারের অধিকাংশ প্রণোদনা, ভর্তুকি, ও নীতি সুবিধা গিয়েছে পোশাক খাতের দিকে। নতুন শিল্প বা প্রযুক্তিনির্ভর খাতগুলো পায়নি প্রয়োজনীয় সহায়তা। ফলে উদ্যোক্তারা ঝুঁকি নিতে সাহস পাননি, আর নতুন খাতগুলোও গতি পায়নি। দ্বিতীয়ত, দক্ষ মানবসম্পদের অভাব। আইটি বা ওষুধ শিল্পে প্রতিযোগিতা করতে হলে প্রযুক্তি, গবেষণা ও উদ্ভাবনে দক্ষ কর্মশক্তি প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের শিক্ষা কাঠামো এখনো তেমনভাবে প্রস্তুত নয়।
বাংলাদেশের জন্য এখন সবচেয়ে জরুরি হলো রপ্তানি কাঠামোর পুনর্গঠন। প্রথমত, তথ্যপ্রযুক্তি খাতকে বড় পরিসরে সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। ভারত ও ফিলিপাইনের মতো দেশগুলো তাদের আইটি ও বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং শিল্প থেকে বছরে বিলিয়ন ডলার আয় করছে। বাংলাদেশের তরুণ কর্মশক্তি এই খাতে প্রতিযোগিতামূলক হতে পারে যদি সরকার ও বেসরকারি খাত মিলে দক্ষতা উন্নয়ন ও অবকাঠামোতে বিনিয়োগ বাড়ায়। দ্বিতীয়ত, কৃষি-প্রসেসিং ও খাদ্য রপ্তানি খাতে বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের কৃষিজ উৎপাদন দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম, কিন্তু ভ্যালু-অ্যাডেড পণ্য রপ্তানি প্রায় নেই বললেই চলে। থাইল্যান্ড বা ভিয়েতনামের মতো আধুনিক কৃষি-প্রসেসিং মডেল গড়ে তোলা গেলে এটি একটি টেকসই বিকল্প হতে পারে। তৃতীয়ত, ফার্মাসিউটিক্যাল, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ও শিপবিল্ডিং খাত ভবিষ্যতের জন্য বড় সম্ভাবনাময়। বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প ইতিমধ্যে আফ্রিকা ও এশিয়ার ১৫টিরও বেশি দেশে পণ্য রপ্তানি করছে, যা রপ্তানি বৈচিত্র্যে ইতিবাচক সংকেত। চতুর্থত, ইউরোপ ও আমেরিকার বাইরেও নতুন বাজারে প্রবেশ করতে হবে, বিশেষ করে আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও পূর্ব এশিয়ায়।
বাংলাদেশের রপ্তানি সাফল্য নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, কিন্তু এক পণ্যের ওপর নির্ভরতা ভবিষ্যতের জন্য বড় ঝুঁকি। বৈচিত্র্যহীন অর্থনীতি কখনো টেকসই হতে পারে না। এখন সময় এসেছে “সস্তা পোশাকের দেশ” থেকে “দক্ষ শিল্পের দেশ” হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার। শুধু শ্রম নয়, আমাদের রপ্তানি হতে হবে জ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনেরও। এই রূপান্তরই হবে বাংলাদেশের পরবর্তী অর্থনৈতিক বিপ্লব।
লেখক :
ইব্রাহীম খলিল (সবুজ)
শিক্ষার্থী, আইন ও ভূমি প্রশাসন অনুষদ,
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ।
